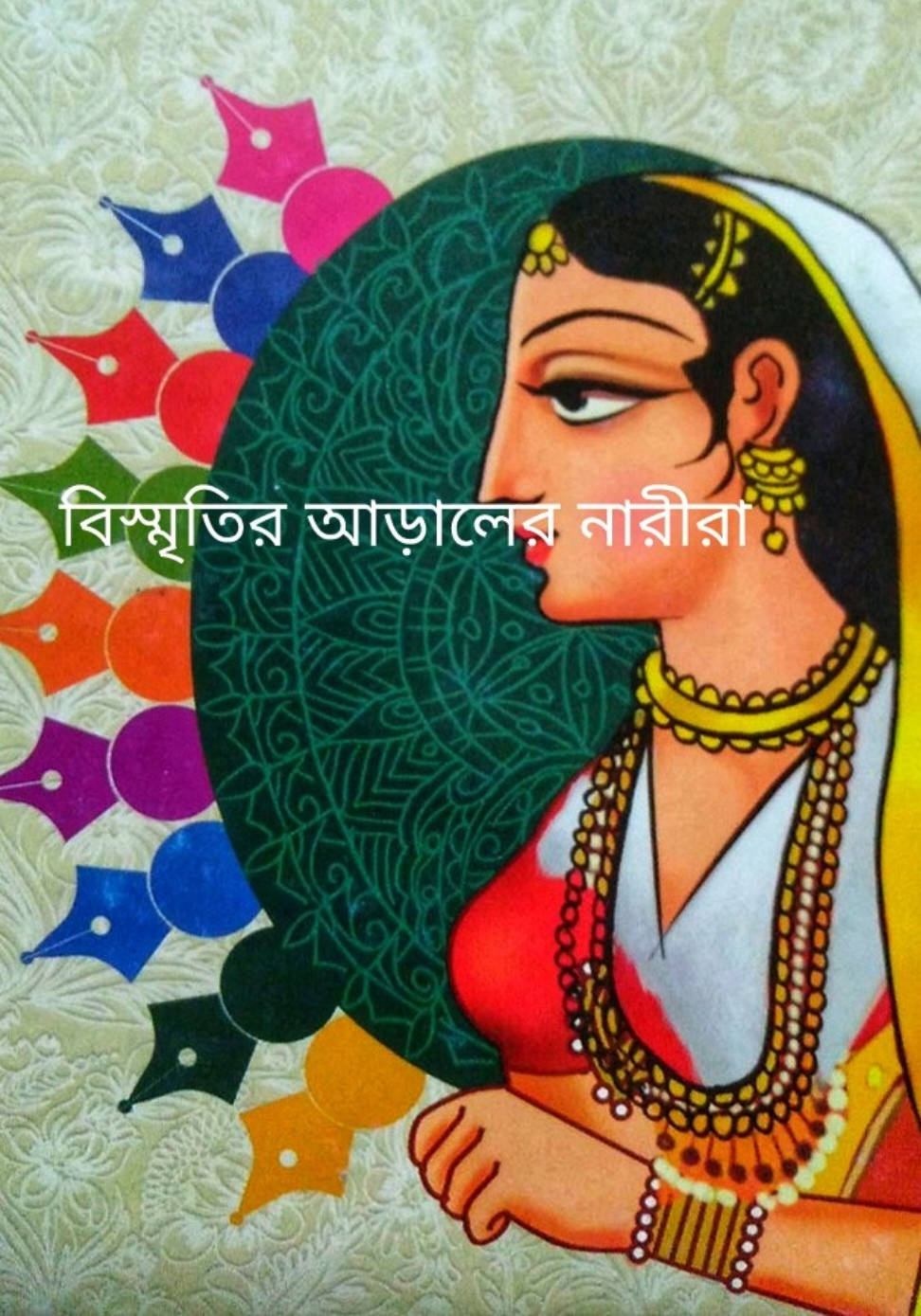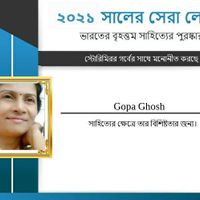বিস্মৃতির আড়ালের নারীরা
বিস্মৃতির আড়ালের নারীরা


এ বছর আমাদের দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হতে চলছে - স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। এই উৎসব নিঃসন্দেহে সেইসব বীরদের স্মরণ করার দিন যাঁরা ইংরেজের অত্যাচারের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে রক্ত-ঘাম ঝরিয়েছেন ও জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন । অথচ 'বীর' নামক বিশেষণ বা 'বীরত্ব' নামক বিশেষণটি শুনলে মানসপটে কোনো না কোনো পুরুষের ছবিই ভেসে ওঠে । স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আজ শাসক দল পুনর্লিখন করছে বটে, তারা মুছে দিচ্ছে সেলুলার জেলে বন্দী বিপ্লবীদের নাম। কিন্তু লক্ষনীয়, এর আগেও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচলিত মূলধারার ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে গেছেন দলিত আদিবাসীরা। তার উপর সেই দলিত-আদিবাসী বিপ্লবীরা যদি নারী হন তো কথাই নেই! লিঙ্গগত প্রান্তিকতার সঙ্গে জাতি-বর্ণগত বা শ্রেণিগত প্রান্তিকতাও এঁদের রেখেছে অন্ধকারের অন্তরালে । এই লেখার মাধ্যমে জানাই সেইসব অবলুপ্ত নামেদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী । আজ দেশের এই বিশেষ সময় তাদের স্মরণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজন বলে মনেকরি।
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দলিত নারীর সংগ্রামের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় অষ্টাদশ শতকের নারী যোদ্ধা কুইলি-র কথা, নবারুণের বেবি কে পারিজাত -এর বেবি-কে-র মতো যিনি মানবীবোমা হয়ে উঠেছিলেন। কুইলি ছিলেন বর্তমান তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গাইয়ের রানি ভেলু নাছিয়ারের সেনাধ্যক্ষা। কিন্তু রানি ভেলু নাছিয়ারকেও কি আমাদের পরিচিত ? এই রানিই প্রথম ভারতীয় শাসক, যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় সাতাত্তর বছর আগে, ১৭৮০ সালে এই যুদ্ধ হয়। যে রণকৌশল তাঁকে জিততে সাহায্য করেছিল, তা তাঁর প্রধান সেনাধ্যক্ষা কুইলির মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। আজও তামিল ভাষায় কুইলিকে কেউ 'বীরথালাপ্যাথি' (সাহসী সমরনায়িকা) বলেন, কেউ বা বলেন 'বীরামঙ্গাই' (সাহসী নারী)। তিনি অরুণথিয়ার তফসিলি জাতিভুক্ত ছিলেন। কুইলির জন্ম হয়েছিল পেরিয়ামুথান এবং রাকু নামের কিষাণ-কিষাণীর ঘরে। মা রাকু বন্য ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে মরেন ফসল বাঁচাতে গিয়ে। বিধ্বস্ত পেরিয়ামুথান তখন কুইলির সাথে শিবগঙ্গাইয়ে চলে যান। সেখানে তিনি মুচির কাজ করতেন। কুইলি তাঁর মায়ের সাহসিকতার গল্প বাপের কাছে শুনে বড় হন। বাপ শীঘ্রই রানি ভেলু নাছিয়ারের গুপ্তচর নিযুক্ত হন। যুদ্ধের সময় তিনিও তাঁর মেয়ে এবং রানির পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিলেন। বাবার কাজের প্রকৃতির ফলেই কুইলি রানি ভেলু নাছিয়ারের ঘনিষ্ঠ হলেন। একাধিকবার রানির জীবন রক্ষা করেছিলেন কুইলি। তাই রানি কুইলিকে তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী করে নেন। যখন ব্রিটিশরা ভেলু নাছিয়ারের পরিকল্পনা জানার জন্য কুইলিকে চাপ দেয়, তখনও তিনি মাথা নোয়াননি। ফলে দলিতরা ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন এবং তাদের বস্তিতে বস্তিতে অত্যাচার ঘনিয়ে আসে।
পরে কুইলি সর্বময় কর্ত্রী হয়ে ওঠেন সেনাবাহিনীর। মারুথু পান্ডিয়ার্স, হায়দার আলি এবং টিপু সুলতানের সাথে সফলভাবে জোট গঠন করে, রানি ভেলু নাছিয়ার তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁদের সেনাবাহিনী সু-প্রশিক্ষিত ছিল এবং কয়েকটি যুদ্ধে তাঁরা জিতেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত উন্নত অস্ত্রের কারণে তাঁরা শেষ পর্যন্ত হেরে যান।
কিন্তু নিজের শক্তি কম থাকলে, তখন লড়াইটা হয় কৌশলের। এই সময় কুইলি সেই পথে গিয়ে শেষ কৌশল প্রয়োগ করেন। শিবগঙ্গাই কোট্টাই (দুর্গ)-এ নবরাত্রির দশম দিনে, রাজরাজেশ্বরী আম্মানের মন্দিরে বিজয়া দশমী উৎসব। সেই উপলক্ষে মহিলাদের দুর্গে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেছিল। কুইলি এই সুযোগকে কাজে লাগালেন। ফুল এবং ফলের ঝুড়ির ভিতরে অস্ত্র লুকিয়ে, মহিলারা দুর্গে প্রবেশ করল এবং রানির ইঙ্গিতে ব্রিটিশদের আক্রমণ করল। অন্যদিকে সৈন্যরা সাধারণ পোষাকে পোশাকে দুর্গের চারদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুইলি ইতিমধ্যেই ব্রিটিশদের অস্ত্রাগারের অবস্থান জেনে নিয়েছিলেন। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সৈন্যদের বলেন, প্রদীপ জ্বালানোর ঘি ও তেল তাঁর উপরেই ঢালতে। তারপর তিনি ব্রিটিশদের অস্ত্রাগারে গিয়ে নিজেকে জ্বালিয়ে সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস করলেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অস্ত্র হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল। তামিলনাড়ু সরকার, প্রায় এক দশক ধরে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর, অবশেষে কুইলির একটি স্মারক তৈরি করেছে শিবগঙ্গা জেলায়।
আবার রানি লক্ষ্মীবাই-এর সহচরী ঝালকারি বাই-এর কথাই ধরা যাক। ঝাঁসির 'দুর্গা দল' বা মহিলা ব্রিগেডের দুঁদে নেত্রী তিনি। তাঁর বরও ঝাঁসির সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন। ঝালকারি তীরন্দাজি আর তলোয়ার চালানোয় প্রশিক্ষিত ছিলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের সাথে তাঁর চেহারায় মিলের কারণে তিনি নিজেকে প্রায়শই রানির 'ডাবল' হিসেবে ব্যবহার করতেন, ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দেওয়ার সামরিক কৌশল হিসেবে। ঝালকারি রানির মতো সাজে সজ্জিত হয়ে ঝাঁসি সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি লক্ষ্মীবাইকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। কিংবদন্তী অনুসারে, যখন ব্রিটিশরা তাঁর আসল পরিচয় জানতে পারে, তখন তারা তাঁকে ছেড়ে দেয় এবং তিনি ১৮৯০ পর্যন্ত দীর্ঘ জীবনযাপন করেন। ঝাঁসির এই 'দুর্গা দল' ছিল আরও অনেক নারীর সংগ্রামের সাক্ষী। মান্দার, সুন্দরী বৌ, মুন্ডারি বাই, মতি বাই- এঁরা কেউ কারও চেয়ে কম যেতেন না। এঁরা অকুতোভয় চিত্তে স্বামীদের যুদ্ধে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি। অলসভাবে বৈধব্য গ্রহণ করতে ছিল এঁদের অনীহা। 'চুড়ি ফরওয়াই কে নেওতা/ সিন্দুর পোছওয়াই কে নেওতা' (চুড়ি ভাঙার আমন্ত্রণ, সিঁদুর মুছে ফেলার আমন্ত্রণ) স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁরা নিজেরাও লড়াই-এ ঝাঁপিয়ে পড়েন।
১৮৫৭ সালের নভেম্বরে সিপাহী বিদ্রোহের কালে সিকান্দারবাগের লখনউয়ের এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল। সিকান্দারবাগে বিদ্রোহীদের হাতে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়দের উদ্ধার করতে আসেন কমান্ডার কলিন ক্যাম্পবেল। সে সময় কোনো এক সিপাহী একটি গাছের উপর থেকে গুলি চালিয়ে একের পর এক ইংরেজ সৈন্যদের মারছিল। যখন ইংরেজরা গাছটি কেটে ফেলল, তখন তারা আবিষ্কার করেছিল যে, গুলি চালানো ব্যক্তি কোনো পুরুষ সিপাহী নয়, পাসি সম্প্রদায়ের এক নারী, যিনি উদা দেবী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মূর্তি আজ লখনউয়ের সিকান্দারবাগে শোভা পায়।
ফোর্বস-মিচেল মহাবিদ্রোহের স্মৃতিচারণে উদা দেবীর সম্পর্কে লিখেছেন: 'তিনি একজোড়া পুরাতন প্যাটার্ন-এর অশ্বারোহী পিস্তলে সজ্জিত ছিলেন। তাঁর বেল্টে তখনও একটি পিস্তল ছিল, তাঁর থলি তখনও অর্ধেক ভরা ছিল গোলাবারুদে। তিনি গাছের মধ্যে তার আশ্রয়স্থল থেকে (সেই আশ্রয়স্থল আক্রমণের আগে অতি যত্নে প্রস্তুত করা হয়েছিল) অন্য পিস্তলটি দিয়ে আধ ডজনেরও বেশি লোককে হত্যা করেছিলেন।'
কিত্তুরের রানি চেন্নাম্মাকে তো কর্ণাটক রাজ্যবাসী 'লোকনায়ক' হিসেবে মেনেছে। পঞ্চমশালী লিঙ্গায়েত (বর্তমানে ওবিসি) জাতির এই রানি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধে, কারণ তিনি স্বত্ববিলোপ নীতি অমান্য করেন। রানি চেন্নাম্মার বিয়ে হয়েছিল কিত্তুরের রাজা মল্লসরজা দেশাইয়ের সাথে, তাঁদের এক পুত্র সন্তান ছিল। ১৮১৬ সালে তার স্বামীর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্রও ১৮২৪ সালে মারা যান। সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, ইংরেজরা ঐ রাজ্য করায়ত্ত করতে চায়।
কিত্তুর চেন্নামা শিবলিঙ্গপ্পা নামে এক দত্তকপুত্রকে গ্রহণ করেন, যা ব্রিটিশদের অপছন্দ ছিল । রানি বলেছিলেন তিনি ইংরেজদের রাজ্য সমর্পণ করবেন না। অগত্যা যুদ্ধ।
ব্রিটিশরা কিত্তুরের রানির কাছে পরাস্ত হয়ে, আর কোন যুদ্ধ হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, রানিকে ঠকায়। দ্বিতীয়বার আরও বেশি বাহিনী নিয়ে তারা প্রতিশোধ নেয়। বারো দিনের যুদ্ধের পর, নিজের লোকদের প্রতারণার কারণে, রানি চেন্নাম্মা পরাজিত ও বন্দী হন। তিনি আজীবন কারাবাস করেন। যদিও তিনি শেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তার প্রথম বিজয় এখনও কিত্তুরে প্রতি বছর 'কিত্তুর উৎসব' -এর সময় উদযাপিত হয়। ২০০৭ সালে অবশ্য ভারতের পার্লামেন্টের কমপাউন্ডে তাঁর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। চেন্নামাকে আজ 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েট' করতে উদগ্রীব আরএসএস-ও। এই প্রয়াস বন্ধ করা আশু প্রয়োজন।
মহাবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্যই ছিল, শুধু উচ্চবর্ণ নয়, শুধু পুরুষ নয়, অবদমিত জাতি তথা শ্রেণীর নারীদেরও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। আরেক দলিত বীরাঙ্গনা ছিলেন মুজাফফরনগর জেলার মুন্ডভার গ্রামের মহাবীরী দেবী। মহাবীরী বাইশজন নারীর একটি দল গঠন করেছিলেন, যাঁরা ১৮৫৭ সালে একসঙ্গে অনেক ব্রিটিশ সৈন্যকে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করে হত্যা করেছিল।
এঁদেরই তো উত্তরসূরী ছিলেন দলিত নারী সাবিত্রীবাই ফুলে, যিনি নিজে অসমসাহসী সমাজ সংস্কারক ও ভারতের প্রথম নারী-স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০-এর দশকে দলিত নারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-বিরোধী এবং অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সুলোচনাবাই ডংরেকে কি আমরা চিনি? ১৯৪২ সালের ২০ জুলাই ঐতিহাসিক 'সর্বভারতীয় বঞ্চিত শ্রেণীর মহিলা সম্মেলনে' (AIDCW) সভাপতিত্ব করতে গিয়ে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে, নারীর শরীরে নারীরই অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেন। এই 'অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাস উইমেনস কংগ্রেস' দলিত নারীবাদের একটি নতুন তরঙ্গের সূচনা করে। রামাবাই আম্বেদকর বা সুলোচনা ডংরেরা তো আগে 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কংগ্রেস'-এর সদস্য ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সম্মেলন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বর্ণবৈষম্যের কারণে। যেমন ১৯৩৭ সালে এআইডব্লিউসি সম্মেলনে, শিক্ষাবিদ জয়বাই চৌধুরি দলিত নারীদের খাদ্যগ্রহণের আলাদা আসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মতাদর্শগতভাবেও, দলিত নারীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং উচ্চবর্ণের মহিলাদের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। পরেরটিতে হিন্দু ঐতিহ্য ঘিরে যে মুগ্ধতা ছিল, যে শোধনবাদ ছিল, তা সুলোচনাবাইদের লড়াইতে ছিল না। তাঁরা লিঙ্গভিত্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বর্ণভিত্তিক- সব রকম নির্যাতনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই শুরু থেকেই শুধু দেশের স্বাধীনতা নয়, তাঁরা জোর দিয়েছিলেন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর, নারীশিক্ষার উপর, শরীরের স্ব-শাসনের উপর। তাঁদের বিরোধিতা ছিল দেশীয় নারী-পুরুষদের দ্বারা বর্ণগত ও জাতিগত শোষণের প্রতিও। নাগপুরের ১৯৪২ সালের ওই সম্মেলন পঁচিশ হাজার দলিত নারীর কাছে তার বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিল।
ড: জয়শ্রী সিং এবং গার্গী বশিষ্ঠ তাঁদের গবেষণাপত্রে, A Critical Insight On Status of Dalit Women In India (2018) লিখেছেন, 'ভারতে দলিত নারীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নীরবে বসবাস করছে।তাদের নিজের শরীর, উপার্জন এবং জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা দরিদ্র, নিরক্ষর, যৌন হয়রানি, বর্ণগত হিংসার শিকার এবং শোষিত।' একই কারণে, স্বাধীনতার সংগ্রামেই হোক বা নারীবাদী সংগ্রামে, এই দলিত নারীদের অবদান মনে রাখা হয়নি। সে ইতিহাস পুনরুদ্ধার করার সময় এসেছে।
আদিবাসী নারীদের কথাই বা মনে রেখেছে কজন? স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে সাঁওতাল - কোল - মুন্ডাদের বিদ্রোহ ছোট ছোট অধ্যায়ে যদি বা লেখা থাকে, জনজাতিগুলির নারী-নেত্রীদের কথা লেখা থাকে কই?
ফুলো মুর্মু এবং ঝানো মুর্মু সিধু কানু চাঁদ ভৈরবের মতো বিখ্যাত হননি। আজ বেঁচে থাকলে তাঁদের হয়ত সন্ত্রাসবাদী বা মাওবাদী নামে ডাকা হত। ফুলো এবং ঝানো পূর্ব ভারতের সাঁওতাল উপজাতির মুর্মু উপগোষ্ঠীর মেয়ে। তাঁদের বসতভূমি আজকের ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, তা ছিল শোষক ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের বিরুদ্ধেও বটে। সাঁওতালরা নিজস্ব দেশ 'দামিন-ই কোহ' স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ১৭৮০ এর দশক থেকে তাঁরা রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ব্রিটিশরা প্রাথমিকভাবে বন পরিষ্কার করে কৃষিকার্যে এবং গবাদি পশু চরানোর কাজে তাঁদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু তারা মহাজন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও এই এলাকায় প্রবেশ করতে উৎসাহ দিয়েছিল বেশি রাজস্বের লোভে। তারপর মহাজন, ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশরা মিলে আদিবাসীদের জমি দখল করতে শুরু করে। কর-খেলাপিদের জমি নিলামে তোলা হয়। জমিদারির বিকাশ ঘটে। সুদূর ভাগলপুরের আদালত ব্যবস্থা কোন স্বস্তি দেয়নি। পুলিশ এবং প্রশাসনের নিম্নস্তরের কর্মীদের দুর্নীতি সাঁওতালদের বঞ্চিত করে। সেই সময় ঝাড়খণ্ডের বারহাইটের কাছে বোগনাদিহে মুর্মু পরিবারের বড়ভাই সিধু দাবি করেন, ঈশ্বর দর্শন দিয়ে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যে শোষণের থেকে মুক্তি কেবল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই সম্ভব। মুর্মুরা দিকে দিকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে শালগাছের শাখা সহ দূত পাঠায়। সে বার্তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চকাটিয়া অঞ্চলে জড়ো হওয়ার জন্য একটি দিন ধার্য করা হয়। সিধুর বক্তৃতায় জনতা উদ্দীপিত হয়। দিগগিহ পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বরত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশ দেন। তাঁকে খুন করে জনজাতি ঘোষণা করে 'ডেলাবন'! (আমাদের যেতে দিন!) ধনুক -তীর, বর্শা, কুড়ুল এবং অন্যান্য শিকারের অস্ত্র নিয়ে তাঁরা জমিদার, মহাজন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শস্যাগার লুট করেন বা আগুন ধরিয়ে দেন। দলটি কলকাতায় ব্রিটিশ সদর দপ্তরে পৌঁছাতে চেয়েছিল। কিন্তু বরহাইট থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে মহেশপুর ছাড়িয়ে তাঁরা আর এগোতে পারেননি। সিধু এবং কানহুকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দশ হাজারেরও বেশি সাঁওতাল নারী-পুরুষ জীবন দিয়েছিলেন। শোনা যায়, ফুলো এবং ঝানো সৈন্যদের শিবিরে ছুটে যান। অন্ধকারে কুড়ুল চালিয়ে একুশ জন ব্রিটিশ সৈন্যকে নির্মূল করেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে উপজাতীয় নারীদল পুরুষদের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করেছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন।
ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুরের গবেষক বাসবী কিরো তাঁর বই 'উলগুলান কি আওরতেঁ' (বিপ্লবের নারী) বইতে আদিবাসী আন্দোলনের আরও অনেক নারীর কথা বলেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহে যেমন ছিলেন ফুলো এবং ঝানো মুর্মু, ১৮৯০-১৯০০ সালের বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহে তেমন ছিলেন মাকি, থিগি, নাগি, লেম্বু, সালি এবং চম্পি। ছিলেন বীরকান মুন্ডা, মাঞ্জিয়া মুন্ডা এবং দুন্দাং মুন্ডাদের স্ত্রীরা। তানা আন্দোলনে (১৯১৪) ছিলেন দেবমণি ওরফে বন্দানি। রোহতাসগড় প্রতিরোধে ছিলেন সিঙ্গি দাই এবং কাইলি দাই। ওরাঁও মহিলারা পুরুষদের পোশাক পরে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, জনজাতির তরুণতর প্রজন্ম ছাড়া আর কেউ সেসব ইতিহাস খোঁড়ার চেষ্টা করছে না আজও।
আবার বিংশ শতকে মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড থেকে ঔপনিবেশিক শাসকদের তাড়ানোর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আদিবাসী রানি গাইদিনলিউ, পণ্ডিত জওহরলাল যাঁকে 'নাগের রানি' নামে ডাকতেন। রানি গাইদিনলিউ কিশোরী বয়সে উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তিনি জেলিয়াগরং উপজাতির রংমেই গোষ্ঠীর রানি। দশ বছর বয়সে তিনি তাঁর খুড়তুতো ভাই হাইপো জাদোনাং-এর প্রভাবে 'হেরাকা' (যার অর্থ 'বিশুদ্ধ') নামে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন, যার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের তাড়িয়ে উপজাতির অধিকার ও সংস্কৃতি ফিরে পাওয়া। জাদোনাংয়ের মৃত্যুর পর।গাইদিনলিউ নিজেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। জেলিয়াংরং উপজাতিকে তিনি ইংরেজদের কর না দিতে বলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তার পক্ষে ছিল। ব্রিটিশরা গাইদিনলিউকে গ্রেপ্তার করে এবং মাত্র ষোলো বছর বয়সে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে তিনি মুক্তি পান। তিনি আজীবন নিজের জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য কাজ চালিয়ে যান, তিনি নাগাদের খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত করার বিরোধী ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে তাম্রপাত্র মুক্তিযোদ্ধা পুরস্কার, ১৯৮২ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৮৩ সালে বিবেকানন্দ সেবা পুরস্কারে ভূষিত হন। মরণোত্তর বিরসা মুন্ডা পুরস্কারেও ভূষিত হন তিনি। একে আদিবাসী, তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নারী, গাইদিনলিউ-কে প্রান্তিক হিসাবে ইতিহাসের মূলস্রোত তাই ভুলে গেছে।
এই লেখার বাইরেও বহু প্রান্তিক নারীরা আজও রয়ে গেছেন অন্ধকারের আড়ালে, যাদের আত্মত্যাগ নিজের অধিকার রক্ষার এই লড়াইটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন - ইতিহাসের পুনর্লিখন যদি হতেই হয় তাহলে যেন এই সুবিচার করা হয় যে সামনের সারিতে উঠে আসেন এই নারীরা।
তথ্য : আন্তর্জাল, "স্বাধীনতার যুদ্ধে দলিত ও আদিবাসী নারী", "দেশভাগ ও বাংলাভাগের ৭৫ বছর নিয়ে কথাবার্তা", উইকিপেডিয়া ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা।