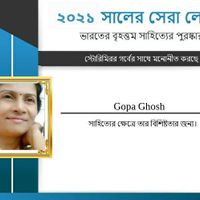শহীদ তিলকা মাঝি
শহীদ তিলকা মাঝি


আমাদের বহু স্বাধীনতার যোদ্ধারা বিস্মৃতির অতলে আজও রয়ে গেছেন, এদের মধ্যে অন্যতম হলেন তিলকা মাঝি। ওনার সীমিত শক্তি, ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে যেভাবে শক্তিশালী ক্ষমতাবান ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে তিনি মাথা উঁচু করে লড়াই করে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন সেটা আজও আমাদের অহংকার। এই দেশপ্রেম আমাদের গর্বের, কিন্তু আমরা কি পারছি তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে?
১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি শাসন লাভ করেছিল। এরপর ১৭৬৯ সালে, সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুর এলাকাটিও চলে গিয়েছিল কোম্পানির শাসনে। যে এলাকাটির পূর্বদিকের পাহাড়গুলিতে বাস করত দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়া উপজাতি। ব্রিটিশদের একদমই পছন্দ করত না পাহাড়িয়ারা। কারণ ব্রিটিশদের প্রশ্রয়েই অরণ্য ও জমির মালিকানা চলে গিয়েছিল বহিরাগত (দিকু) জমিদারদের কাছে। পাহাড়িয়া ও অন্যান্য উপজাতিরা হয়ে গিয়েছিল ভূমিহীন কৃষক। দিকু জমিদারদের কাছ থেকে নিজেদের জমিই ভাড়া নিয়ে চাষ করতে হত। জমির ফসলের সিংহভাগই ঢুকত জমিদারের গোলায়।
১৭৭০ সালে ভয়াবহ খরার প্রকোপে পড়েছিল এলাকাটি। যার পরিণতিতে দেখা দিয়েছিল নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। দিশেহারা হয়ে চারদিক থেকে রাজমহল পাহাড়ের দিকে পালিয়ে আসতে শুরু করেছিল নানা উপজাতির মানুষেরা। কালক্রমে এলাকায় সংখ্যাগুরু হয়ে গিয়েছিল সাঁওতাল উপজাতির মানুষেরা। পাহাড়িয়া হয়ে গিয়েছিল সংখ্যালঘু।
এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল ব্রিটিশরা। কাজে লাগিয়েছিল তাদের কুখ্যাত ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি’। উপজাতিগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কারণ তারা জানত এই এলাকায় রাজত্ব করতে হলে স্বাধীনচেতা উপজাতিদের জোটবদ্ধ হতে দেওয়া চলবে না। এই কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ক্লিভল্যান্ড সাহেব।
অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড ছিলেন ভাগলপুর, মুঙ্গের ও রাজমহলের কালেক্টর সাহেব। ধুরন্ধর ব্রিটিশ অফিসার ক্লিভল্যান্ড এলাকায় পা দিয়েই শিখে নিয়েছিলেন বিভিন্ন উপজাতির ভাষা। ক্ষুব্ধ পাহাড়িয়া উপজাতির প্রধানদের খাজনা মকুব করে দিয়েছিলেন। পাহাড়িয়া উপজাতির যুবকদের নিয়ে ব্রিটিশ সেনার একটি বিভাগও তৈরি করেছিলেন ক্লিভল্যান্ড সাহেব। যা ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল এলাকাটির সমতলে থাকা সাঁওতাল সহ অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়কে। কারণ তারা সবরকম সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল ।
উপজাতিদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার এই ঘৃণ্য কৌশল ধরে ফেলেছিলেন এক স্বাধীনচেতা সাঁওতাল যুবক। পলাশ ফুলের মতো লাল চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন ব্রিটিশদের দিকে। ব্রিটিশদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছিল সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। শালবনে জ্বালিয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম আগুন। যে আগুন একদিন দাবানল হয়ে গ্রাস করেছিল ব্রিটিশদের। গণবিদ্রোহের এই মহানায়কের নাম জাবরা পাহাড়িয়া ওরফে তিলকা মুর্মু।
বর্তমান বিহারের সুলতানগঞ্জ এলাকার তিলকপুর গ্রামে, ১৭৫০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জন্ম নিয়েছিলেন তিলকা মুর্মু। ছোটবেলা থেকেই তিলকা ছিলেন দুঃসাহসী। গ্রামে তাঁর মত বীর ছিল না। এছাড়া গ্রামের যেকোনও সমস্যার সমাধানও করতেন তিলকা। কারণ গ্রামে তাঁর কথাই ছিল শেষকথা। তাই যুবক তিলকা কালক্রমে হয়ে গিয়েছিলেন গ্রামের মুখিয়া বা মাঝি। আশেপাশের গ্রামের মানুষেরা তাঁকে চিনত তিলকা মাঝি নামে।
গ্রামের প্রধান হলেও, অন্যান্য উপজাতীয় প্রধানদের মতো ইংরেজ ও দিকু জমিদারদের বশ্যতা মেনে নেননি তিলকা। কারণ তিনি শৈশব থেকে দেখে এসেছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর ইংরেজ ও জমিদারদের অকথ্য নির্যাতন। তাই এক সন্ধ্যায়, ঘন অরণ্য ঘেরা গ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে তিলকা মাঝি হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন, অরণ্য ও জমির মালিক আমরা, ভূমিপুত্ররা। তাই দিকুদের (বহিরাগত) হাত থেকে অরণ্য ও জমির অধিকার ছিনিয়ে নিতেই হবে।” তিলকা জানতেন সে ক্ষমতা আদিবাসীদের আছে। কারণ এর আগে জোটবদ্ধ হয়ে আদিবাসীরা এলাকাছাড়া করেছিল মারাঠা ও মোগলদের।”
এলাকার ভূমিহীন নিপীড়িত আদিবাসীরা সাড়া দিয়েছিল তিলকা মানঝির ডাকে। কারণ ব্রিটিশদের কৌশলে লাভবান হচ্ছিল উপজাতির প্রধানেরা। কিন্তু সাধারণ আদিবাসীদের ঘিরে ফেলেছিল খাজনার চোরাবালি। এছাড়াও অবাধে চলছিল আদিবাসীদের জমি লুঠ ও নারীদের ওপর লাঞ্ছনা। ফলে বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিলেন তিলকা মাঝি। প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ব্রিটিশ ও তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নামার।
তিলকা মাঝির বিদ্রোহ ঘোষণার কথা পৌঁছে গিয়েছিল ইংরেজদের কাছে। তিলকাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু রাজমহল পাহাড় যাঁর হাতের তালুর মতো চেনা, তাঁকে ধরে কার সাধ্য! ব্রিটিশ চরদের নজর এড়িয়ে তিলকা রাতের অন্ধকারে পৌঁছে যেতেন আদিবাসীদের গ্রামে। আবেগমথিত ভাষণ দিয়ে একত্রিত করার চেষ্টা করতেন আদিবাসীদের।
এভাবেই একদিন তিলকা পৌঁছে গিয়েছিলেন ভাগলপুর। সভায় উপস্থিত বিশাল সংখ্যক আদিবাসীর মধ্যে তিলকা বিতরণ করেছিলেন হাজার হাজার শালপাতা। যে শালপাতা গুলিতে লেখা ছিল,”হারানো অধিকার আদায়ের জন্য, আমাদের জোটবদ্ধ হতেই হবে।” সেদিনের জনসভায় তিলকা মাঝির রক্তগরম করা ভাষণ, রক্তের কণায় কণায় বাজিয়েছিল স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার দামামা।
এরপর গণবিদ্রোহের নেতা তিলকা মাঝি, গড়ে তুলেছিলেন অরণ্যযুদ্ধে পটু এক দুর্ধর্ষ আদিবাসী গেরিলাবাহিনী। সম্বল ছিল তির ধনুক, তরবারি, বল্লম, টাঙ্গি ও গুলতি। এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশবাহিনীকে হারাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিলকা। বাহিনীর প্রত্যেকটি যোদ্ধাকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তিলকা নিজেই। তারপর রাতের অন্ধকারে, ক্ষুধার্ত হায়নার মতো হানা দিতে শুরু করেছিলেন, ব্রিটিশ ক্যাম্প, কোষাগার ও জমিদারবাড়িগুলির ওপর।
১৭৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে, প্রায় তেরোশো আদিবাসী গেরিলা নিয়ে তিলকা হানা দিয়েছিলেন রামগড়ের ব্রিটিশ ক্যাম্প ও সরকারি কোষাগারে। তিলকা মাঝির এই দুঃসাহসী অভিযানের সঙ্গী ছিলেন রমনা পাহাড়ি ও কারিয়া পুজহরের মত উপজাতি প্রধানেরা। সরকারি কোষাগার ও ক্যাম্প থেকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র লুঠ করেছিলেন বীরযোদ্ধা তিলকা। লুঠ করা অর্থ তিলকা বিলিয়ে দিয়েছিলেন গরীব আদিবাসীদের মধ্যে। এলাকার আদিবাসীদের কাছে তিলকা মানঝি হয়ে গিয়েছিলেন ‘বাবা তিলকা’। যদিও ব্রিটিশ পুলিশের খাতায় গণবিপ্লবের মহানায়ক তিলকার নামের পাশে লেখা হয়েছিল ‘কুখ্যাত ডাকাত’।
তিলকা মাঝির এই একটি অভিযানেই কেঁপে উঠেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এলাকায় জারি হয়েছিল সেনা শাসন। আদিবাসীদের নয়নমণি তিলকাকে খতম করার লক্ষ্য নিয়ে রাজমহল পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিল ৮০০ সেনা। নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্রুক। শুরু হয়েছিল ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে তিলকা মাঝির গেরিলা বাহিনীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ইংরেজ বাহিনীর বন্দুক ও কামান হামলায় তিলকা হারিয়েছিলেন তাঁর প্রচুর সহযোদ্ধাকে। কিন্তু তবুও দমানো যায়নি তিলকা মাঝিকে।
জনসমর্থনের হাওয়ায় ১৭৮৩ সালে দাবানল হয়ে উঠেছিল, বাবা তিলকার “শালগিরা” বিদ্রোহ। ব্রিটিশ সেনা ঘিরে ফেলেছিল সুলতানগঞ্জ ও ভাগলপুরের সব পাহাড়। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়্গুলিতে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা। খাদ্য ও অন্যান্য রসদ পাহাড়ে না পৌঁছানোর ফলে সমস্যায় পড়েছিলেন তিলকা। প্রায় অনাহারে থেকেও চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে ব্রিটিশদের চক্রব্যূহ থেকে বের হতে চাই ছিলেন আদিবাসী আন্দোলনের মহানায়ক, অরণ্যের বরপুত্র তিলকা।
১৭৮৪ সালের ১ জানুয়ারি, সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি স্বচক্ষে দেখার জন্য পাহাড়ের কাছে গিয়েছিলেন ক্লিভল্যান্ড সাহেব। নিজের বীরত্ব জাহির করার জন্য, ঘোড়ায় চড়ে চলেছিলেন সবার আগে। কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলছিল পিস্তল। পাহাড় থেকে ক্লিভল্যান্ডের ঘোড়া তখন ছিল বেশ কিছুটা দূরে। অতর্কিতে ঘন অরণ্যের বুক চিরে উড়ে এসেছিল পালক গাঁথা তির। ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছিলেন তীরবিদ্ধ ক্লিভল্যান্ড সাহেব। অরণ্যের কিনারায় থাকা একটি খেজুর গাছের ওপর থেকে তীরটি ছুঁড়েছিলেন তিলকা মাঝি। আহত ক্লিভল্যান্ড সাহেবকে ইংল্যান্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
ক্লিভল্যান্ডের ওপর আক্রমণ অপ্রত্যাশিত ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। তিলকাকে ধরার জন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার সেনা পাঠিয়েছিল ব্রিটিশেরা। গোয়েন্দারা খবর এনেছিল তিলকার বেশিরভাগ সাথী যুদ্ধে মৃত বা আহত। তিলকা নিজেও আহত, কিছু বিশ্বস্ত সঙ্গীকে নিয়ে তিনি লুকিয়ে আছেন তিলাপুর অরণ্যে।
কিন্তু অরণ্যের ভেতরে গিয়ে তিলকাকে ধরা আনা, জলে নেমে কুমীরকে ডাঙায় তোলার থেকেও কঠিন। তাই ব্রিটিশেরা নিয়েছিল অন্য কৌশল। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে এসেছিল কিছু আদিবাসীকে। যারা তিলকার গেরিলাদের কাছে খাবার ও ওষুধ পৌঁছে দিয়ে আসত। আদিবাসী সংগ্রামের মহানায়কের সঙ্গে এই মানুষগুলিই করেছিল চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ব্রিটিশদের জানিয়ে দিয়েছিল আহত তিলকার ঠিকানা।
১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসেই, বিশাল বাহিনী নিয়ে বাবা তিলকার গোপন ডেরায় অতর্কিতে হানা দিয়েছিলেন ব্রিটিশ কম্যান্ডার আয়ারকুট। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিলকা। তিনি কল্পনাতেও আনতে পারেননি, আদিবাসী সম্প্রদায়ের কেউ এভাবে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।
কিন্তু তাঁর নামও তিলকা মাঝি। বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করবেন। কাপুরুষের মত ধরা দেবেন না। তাই আহত চিতাবাঘের গতিতে তিলকা শুরু করেছিলেন জীবনের শেষ যুদ্ধ। তবে অসম যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তিলকা। গুলির পুরনো ক্ষত বিষিয়ে যাওয়ায় পালাবার ক্ষমতা ছিল না তিলাকার। তাই একসময় ব্রিটিশ সেনার হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন আদিবাসী বিদ্রোহের মহানায়ক তিলকা মাঝি।
পায়ে দড়ি বেঁধে ঘোড়া দিয়ে তিলকা মাঝিকে টানতে টানতে নিয়ে আসা হয়েছিল ভাগলপুর। পথের ধুলোয় মিশে গিয়েছিল বাবা তিলকার ক্ষতবিক্ষত শরীর থেকে ঝরে পড়া রক্ত। তবুও সামান্যতম কাতরোক্তি শুনতে পাননি কেউ। তিলকার চোখ দুটো তখনও জ্বলছিল তীব্র আক্রোশ ও ঘৃণায়। সেই দৃশ্য দেখা প্রতিটি আদিবাসী সে দিন মনে মনে নিয়েছিলেন শপথ,” বাবা তিলকা, তোমার ঝরা রক্তের প্রতিটি কণার বদলা একদিন আমরা নেবই।”
১৭৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি, ইংল্যান্ডে ফেরার সময় জাহাজেই প্রাণ হারিয়েছিলেন তিলকার তীরে আহত ক্লিভল্যান্ড সাহেব। এর ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি, মৃত অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ডের ভাগলপুরের বাংলোর সামনে থাকা বটগাছটির ডালে, ঝোলানো হয়েছিল ফাঁসির দড়ি। উপস্থিত কয়েকহাজার আদিবাসীর সামনে মাথা উঁচু করে ফাঁসির দড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ বছরের বাবা তিলকা মাঝি।
মৃদু হেসেছিলেন জনতার দিকে তাকিয়ে। জনতার জলভরা চোখে বাবা তিলকা দেখেছিলেন ক্রোধের বাষ্প। অনুভব করেছিলেন, তাঁকে হত্যা করতে সফল হলেও, তাঁর জ্বালানো শালগিরার আগুনকে কোনদিনই নেভাতে পারবে না ব্রিটিশরা। সেই আগুনে ঝলসে যেতেই হবে ব্রিটিশদের। আজ নয়ত কাল। তাই হাসিমুখেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিয়েছিলেন বাবা তিলকা।
বাবা তিলকার স্বপ্ন একদিন সত্যি হয়েছিল। ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে দিকে দিকে শুরু হয়েছিল আদিবাসী বিদ্রোহ। তিলকা মাঝির দেখানো পথেই একদিন ইতিহাস গড়েছিল তামাড় বিদ্রোহ (১৭৮৯), প্রথম ভূমিজ বিদ্রোহ (১৭৯৮), চুয়াড় বিদ্রোহ( ১৭৯৯), ভিল বিদ্রোহ (১৮০০), চেরো বিদ্রোহ (১৮১০),মুন্ডা বিদ্রোহ ( ১৮১৯), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১), দ্বিতীয় ভূমিজ বিদ্রোহ (১৮৩৪) ও সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)। তৈরি করে দিয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত।
এরপর, ১৮৫৭ সালে, ব্রিটিশ অপশাসনের কফিনে শেষ পেরেকটি মেরেছিলেন, বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সিপাহী মঙ্গল পান্ডে। ইতিহাসের পাতায় আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে বালিয়া জেলার, নাগওয়া গ্রামের মঙ্গল পাণ্ডের নাম। কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক গর্জে ওঠার আশি বছর আগে, ব্রিটিশদের দিকে শিস দিয়ে উড়ে গিয়েছিল এক আদিবাসী যুবকের বিষাক্ত তীর।
ভাগলপুর শহরে, তাকে যেখানে হত্যা করা হয় সেই স্থানে তার একটি মুর্তি স্থাপিত আছে। তার সম্মানে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হয় তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সাঁওতাল পরগনার সদর শহর দুমকাতে তার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।
তাকে কি মনে রেখেছে ভারতের ইতিহাস!
তথ্যসূত্র: আন্তর্জাল, উইকিপেডিয়া ও বিভিন্ন পত্রিকা।