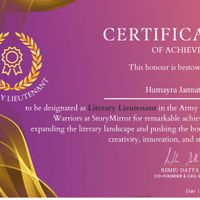মেঘনাদ সাহা
মেঘনাদ সাহা


মেঘনাদ সাহা এফআরএস (৬ অক্টোবর ১৮৯৩ – ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি গণিত নিয়ে পড়াশোনা করলেও পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়েও গবেষণা করেছেন। তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তার আবিস্কৃত সাহা আয়নীভবন সমীকরণ নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মগুলো ব্যাখ্যা করতে অপরিহার্য। তিনি ভারতে নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানে আধুনিক গবেষণার জন্য ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠা করেন। পদার্থবিজ্ঞানে তার অবদানের জন্য ১৯২৭ সালে লন্ডনের রয়াল সোসাইটি তাকে এফআরএস নির্বাচিত করে।
তিনি ও তার সহপাঠী এবং সহকর্মী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম আলবার্ট আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার সূত্রকে জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। স্বনামধন্য এই পদার্থবিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ধারায় পঞ্জিকা সংশোধন করেন। এছাড়া ভারতের নদীনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ভারতে পদার্থবিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের জন্য ১৯৩১ সালে ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স, ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ১৯৩৪ সালে ভারতে পদার্থবিজ্ঞানীদের সংগঠন ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটিও প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্যোগেই ভারতে ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অব সায়েন্সের সূচনা হয়, যা বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অব টেকনোলজি (আই.আই.টি.) নামে পরিচিত।
১৯৫২ সালে ভারতীয় লোকসভার নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র (বর্তমানে কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র) থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সাংসদ হন।
মেঘনাথ সাহা ৬ অক্টোবর, ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার অন্তর্গত শেওড়াতলী গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জগন্নাথ সাহা ও মাতার নাম ভুবনেশ্বরী সাহা। তিনি ছিলেন পঞ্চম সন্তান।তার পিতা ছিলেন পেশায় মুদি।
তৎকালীন সময়ের ধর্মগোড়া উচ্চ-অহংকারী ব্রাহ্মণদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের কারণে এবং শৈশব-কিশোর এবং কর্মজীবনে জাতপাতের শিকার হওয়ায় তার হৃদয়ে বৈদিক হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছিল।
গ্রামের টোলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। সেই সময় তার গ্রামের বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখার করার সুযোগ ছিল। তার পিতা ছোটবেলায় তার বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা দোকানের কাজ শেখা আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু তার দাদা জয়নাথ এবং তার মায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তার ইতিহাস এবং গণিতের মেধার কথা তার পিতার কাছে অবগত করলে তার পিতা তাকে হাই স্কুলে ভর্তি করতে সম্মত হন। এরপর তিনি শেওড়াতলী গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে শিমুলিয়ায় মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে (মিডল স্কুল - ব্রিটিশ আমলে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি পড়ার স্কুল) ভর্তি হন। এত দূরে প্রতিদিন যাওয়া আসা করে তার পক্ষে পড়াশোনা করা দুরূহ হওয়ার পাশাপাশি মেঘনাদের বাবার পক্ষেও আর্থিক সামর্থ্য ছিল না শিমুলিয়া গ্রামে মেঘনাদকে রেখে পড়ানোর। তখন মেঘনাদের বড় ভাই এবং পাটকল কর্মী জয়নাথ শিমুলিয়া গ্রামের চিকিৎসক অনন্ত কুমার দাসকে মেঘনাদের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করায় তিনি রাজি হন। সেখানে তিনি শিমুলিয়ার ডাক্তার অনন্ত নাগের বাড়িতে থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ লাভ করেন। এই স্কুল থেকে তিনি শেষ পরীক্ষায় ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান।
এরপর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে সারাবাংলা উত্তাল হয়েছিল। সেই সময় তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য তৎকালীন গভর্নর বামফিল্ড ফুলার আসলে মেঘনাথ সাহা ও তার সহপাঠীরা বয়কট আন্দোলন করেন। ফলত আন্দোলনকারী সহপাঠীদের সাথে তিনিও বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন এবং তার বৃত্তি নামঞ্জুর হয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী কিশোরীলাল জুবিলি হাই স্কুলের একজন শিক্ষক স্বঃপ্রণোদিত হয়ে তাকে তাদের স্কুলে ভর্তি করে বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকেই তিনি ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মাসিক ৪ টাকার সরকারি বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় গণিত এবং ভাষা বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর অধিকার করে।
বিদ্যালয় শিক্ষার পর তিনি ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বৈশ্য সমিতির মাসিক দুই টাকা বৃত্তিও লাভ করেন। সেই সময় তিনি কলেজের রসায়নের শিক্ষক হিসেবে হরিদাস সাহা, পদার্থবিজ্ঞানে বি এন দাস এবং গণিতের নরেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কে পি বসু সহ প্রমুখ স্বনামধন্য শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি বিজ্ঞান ছাড়াও ডক্টর নগেন্দ্রনাথ সেনের কাছে জার্মান ভাষার প্রশিক্ষণ নেন। এই বিদ্যালয় থেকে তিনি আই এস সি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।
১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে গণিতে অনার্স নিয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় ১৯১১-১৯১৩ সাল পর্যন্ত দু'বছর ইডেন ছাত্রাবাস এবং পরে একটি মেসে থেকে পড়াশোনা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ, সুরেন্দ্র নাথ মুখার্জী প্রমূখ তার সহপাঠী ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সংখ্যাতত্ত্ব বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এক বছরের এবং রসায়নবিদ নীলরতন ধর দুই বছরের সিনিয়র ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি গণিতের অধ্যাপক হিসাবে বি এন মল্লিক এবং রসায়নে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং পদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুকে পেয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ সালে গণিতে সম্মানসহ স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম হন।
মেঘনাদ ১৯২৮ সালে তার সমস্ত গবেষণার ফলাফল একত্র করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রির জন্য আবেদন করেন। তার সব গবেষণা বিবেচনা করার জন্য উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার থিসিস পেপার বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বিদেশে অধ্যাপক ডাবলু রিচার্ডসন, ডঃ পোর্টার এবং ডঃ ক্যাম্বেল তার থিসিস পেপার পর্যালোচনা করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯১৯ সালে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করে। একই বছর মেঘনাদ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। যার ফলে তিনি ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে গবেষণার সুযোগ পান।
ভাষায় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সর্বপ্রথম অনুবাদ। প্রিন্সটনের আইনস্টাইন আর্কাইভে তাদের অনুবাদের একটি প্রত্যায়িত রাখা আছে।
১৯১৭ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোন প্রবীণ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধান ছাড়াই তিনি লন্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন ও ফিজিক্যালি রিভিউ জার্নালে তার মৌলিক গবেষণা গুলি প্রকাশ করেন। বিকিরণ চাপ সম্পর্কিত গবেষণা জন্য ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে অন হার্ভার্ড ক্লাসিফিকেশন অফ স্টেলার স্পেক্ট্রাম গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং বিদেশে গবেষণার সুযোগ পেয়ে যান।
এরপর ১৯১৯ সালে তিনি প্রথম পাঁচ মাস লন্ডনে বিজ্ঞানী আলফ্রেড ফাউলারের পরীক্ষাগারে এবং পরবর্তীতে বার্লিনে ওয়াস্টার নার্নস্টের সাথে কাজ করেন।
মেঘনাদ সাহা ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে তার গবেষণা লব্ধ তাপীয় আয়নায়ন তত্ত্ব বিষয়ে Ionisation of the solar chomosphere শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। তার গবেষণাটি মূলত উচ্চ তাপমাত্রায় আয়নায়ন তত্ত্ব ও নক্ষত্রের আবহমন্ডলে তার প্রয়োগ নিয়ে।
তিনি ইউরোপ যাত্রার আগে Ionisation of the solar chromospher and on the Harvard classification of steller spectra গবেষণাপত্র দুটি প্রকাশের জন্য Philosophical Magazine এর কাছে পাঠান কিন্তু সেখানে ফাউলারের গবেষণাগারে থাকাকালীন হার্ভার্ড গ্রুপ ছাড়াও নক্ষত্রের শ্রেণীবিভাগে লাইকার ও ছাত্রদের অবদান সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর তিনি আরো কিছু নতুন তথ্য দিয়ে তার দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি সম্প্রসারিত করেছেন। যা On the physical theory of steller sprectra শিরোনামে লন্ডনের রয়েল সোসাইটি পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তার এই কাজটি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করা হয়। এস রজল্যান্ড তার Theoretical Astrophysics গ্রন্থে তার গবেষণার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।
১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে খয়রা অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সেই সময় তৎকালীন আচার্য ও গভর্নরের সঙ্গে উপাচার্যের মতবিরোধ থাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে সহকারী পাননি। সেকারণে গবেষণার জন্য তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক নীলরতন ধরের আগ্রহে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ভালো পরিমণ্ডল না থাকা সত্ত্বেও তার চেষ্টায় তিনি একটি গবেষণা দল করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, পরমাণু ও অণুর বর্ণালী, নেগেটিভ ইলেক্ট্রন অ্যাফিনিটি, অণুর উষ্ণতাজনিত বিভাজন, আয়নোস্ফিয়ারে রেডিও তরঙ্গের গতিবিধি, উচ্চতর আবহমণ্ডল ইত্যাদি। তিনি তাপীয় আয়নন তথ্য পরীক্ষার জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন।
১৯৩১ সালে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি থেকে তিনি ১৫০০ পাউন্ড আর্থিক সাহায্য পান, তা দিয়ে তিনি আয়নতত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ করেন।
১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সাইন্স কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ইতালিতে সরকারের আমন্ত্রণে ভোল্টার শতবার্ষিকী উৎসবে আমন্ত্রিত হন এবং মৌলিক পদার্থের মৌলিক পদার্থের জটিল বর্ণালির ব্যাখ্যা সম্পর্কে গবেষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কারনেসি ট্রাস্টের ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐসময় তিনি জার্মানি, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা পরিদর্শন করেন। সেই সময় হার্ভার্ড কলেজের ল্যাবরেটরীতে এইচ শেফ্লির সাথে গবেষণা করেন।
তিনি মিউনিখে থাকাকালীন জার্মান একাডেমি সংবর্ধনা পান। আমেরিকায় লরেন্সের সাইক্লোট্রন যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করেন। যা পরবর্তীতে ভারতবর্ষে সাইক্লোট্রন তৈরিতে সাহায্য করেছে।
কোপেনহেগেন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কনফারেন্সে পরমাণু বিভাজনের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হন যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গবেষণাগার তৈরিতে তাকে সাহায্য করেছে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় সাইন্স কংগ্রেস জুবিলী অধিবেশনে এরিংটন কলকাতা আসেন। তিনি মেঘনাথ সাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন তার মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জন্য একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্ণ গবেষণাগার থাকা উচিত। তিনি আরো বলেন তার আবিষ্কার গ্যালিলিওর দূরবীন আবিষ্কারের পর সেরা ১০টি আবিষ্কারের মধ্যে একটি।পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে ব্যাঙ্গালোরে ভারতে এই ধরনের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে মেঘনাথ সাহা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এলাহাবাদে থাকাকালীন তিনি আয়নোস্ফিয়ার গবেষণা করেছিলেন। কলকাতায় এসেও তিনি তা পুনরায় শুরু করেন। কিন্তু তার সহকর্মী ও ছাত্র শিশির কুমার মিত্রের পরিচালনায় রেডিওফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ গঠিত হয় এবং সেখানে আয়নোস্ফিয়ার গবেষণার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ থাকায় তিনি আর আয়োনোস্ফিয়ার নিয়ে গবেষণা করেন নি। কারণ তিনি মনে করতেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি দুটি একই ধরনের গবেষণা কাজ করা নিরর্থক।
কলকাতা ফিরে আসার পর তার গবেষণার মূল বিষয় ছিল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। তিনি বার্কলের লরেন্সের সাইক্লোট্রন ল্যাবরটরি পরিদর্শন করার পরেই ভারতেও অনুরূপ সাইক্লোট্রন তৈরীর পরিকল্পনা করেন। এলাহাবাদে সেই সুযোগ না থাকায় তিনি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। কলকাতায় তিনি পুনরায় পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার ছাত্র ও সহকর্মী বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরীকে পিএইচডি ডিগ্রি করার জন্য লরেন্সের কাছে পাঠান। একই সাথে উদ্দেশ্য ছিল সাইক্লোট্রন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তার সাহায্যে সাইক্লোট্রন ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অটো হান ও মিনারের পরমাণু বিভাজন গবেষণা সফল হলে তিনি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আরো বেশি আগ্রহী হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পাঠ্যসূচিতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স অন্তর্ভুক্ত করেন। টাটা ট্রাস্টের অনুদান এবং বিধানচন্দ্র রায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রন তৈরীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে নাগ চৌধুরী ভারতে ফিরলে সাইক্লোট্রন তৈরি প্রাথমিক উপকরণ হিসাবে শক্তিশালী চৌম্বক তামার পাত পৌঁছে যায়। কিন্তু যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকুয়াম পাম্প গুলি যে জাহাজে আসছিল তা জাপানি টর্পেডো আঘাতে ডুবে যায়। সেই সময় তিনি অন্য উপায় না দেখে সিএসআইআরের (CSIR) অনুদানে ভ্যাকুয়াম পাম্প তৈরীর পরিকল্পনা নেয়। {\displaystyle 10^{-5}}{\displaystyle 10^{-5}} মিমি পারদ চাপের ভ্যাকুয়াম পাম্প তৈরি করলেও সাইক্লোট্রন এর উপযোগী বড় পাম্প তৈরি করা সম্ভব হয়নি।
১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মেঘনাথ সাহা ভারতে বায়োফিজিক্স গবেষণার সূত্রপাত করেন। এরপর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নীরজনাথ দাশগুপ্ত তার তত্ত্বাবধানে ভারতে প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেন।এরপর তিনি ভারতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউট তৈরীর কাজে ব্রতী হন। ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে পদার্থবিজ্ঞানে ট্রেনিং দেওয়া ও মৌলিক গবেষণা করা। তিনি মারা যাবার আগে পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর বিজ্ঞান বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন।
মেঘনাথ সাহা ২৪ বছর বয়সে ফিলোসফিক্যাল মাগাজিনে “On Maxwell’s Stress” শিরোনামে তার প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তিনি কমবেশি ৮০ টি মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি তার সবকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাই ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করেছেন। এরমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের পালিত গবেষণাগার এবং ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স অন্যতম। এছাড়া তিনি বিদেশে ফাউলার এবং নার্নস্টের গবেষণাগারে কিছুদিন গবেষণা করলেও সেখানে কোন বিজ্ঞানী সহযোগিতায় একটাও গবেষণাপত্র প্রকাশ করেননি। তার গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান। এই বিষয়ে তিনি আয়নন তত্ত্ব এবং নক্ষত্রের শ্রেণিবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এছাড়াও বিকিরণ তাপ, পরমাণু বিজ্ঞান, তাপগতিতত্ত্ব, বর্ণালী বিজ্ঞান এবং আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কিত অনেক গবেষণা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি পরমাণু ও নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা করেন এবং ভারতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করায় উৎসাহী হন। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পরমাণু বিজ্ঞান, জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা, নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা, আয়ন মণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশবিজ্ঞান, পঞ্জিকা সংস্কার, বন্যা প্রতিরোধ ও নদী পরিকল্পনা সহ নানা বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনামূলক নিবন্ধ লিখেছেন।
মেঘনাদ এবং সত্যেন বোস যুগ্মভাবে সর্বপ্রথম আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সহ তার বিভিন্ন নিবন্ধ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। আইনস্টাইনের ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত মোট যতগুলি নিবন্ধ জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল তার সবগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ শুরু করেন মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাদের এই অনুবাদ ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রিন্সিপাল্স অব রিলেটিভিটি নামে প্রকাশিত হয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অনূদিত বইটির ভূমিকা লেখেন। ১৯৭৯ সালে আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আইনস্টাইনের নিবন্ধগুলির প্রথম অনুবাদ জাপানে প্রকাশিত হয়েছিল বলা হয়। নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই ভ্রম সংশোধিত হয় এবং মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অনুবাদই আইনস্টাইনের রচনার প্রথম অনুবাদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে তাদের এই অনূদিত প্রিন্সিপাল্স অব রিলেটিভিটির একটি প্রতিলিপি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনস্টাইন আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাদের এই অনূদিত গ্রন্থটিই হলো সারাবিশ্বে আইনস্টাইনের রচনার প্রথম অনুবাদ।
১৯৩০ সালে ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী দেবেন্দ্র মোহন বসু এবং শিশির কুমার মিত্র মেঘনাদ সাহাকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করেন। নোবেল কমিটি মেঘনাদ সাহার কাজকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হিসেবে বিবেচনা করলেও এটি "আবিষ্কার" নয় বলে তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। মেঘনাদ সাহাকে ১৯৩৭ সালে এবং ১৯৪০ সালে আর্থার কম্পটন এবং ১৯৩৯, ১৯৫১ ও ১৯৫৫ সালে শিশির কুমার মিত্র আবারো মনোনীত করলেও নোবেল কমিটি তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে।
১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এ সময় তিনি তার কর্মস্থল ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভবনের পরিকল্পনা কমিশনের দিকে যাচ্ছিলেন; এমন সময় পড়ে যান। হাসপাতালে নেবার পর স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে মারা যান। রিপোর্টে বলা হয়: তিনি মারা যাবার ১০ মাস আগে থেকে উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তাকে পরের দিন কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশান এ দাহ করা হয়।