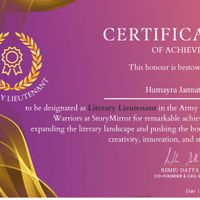বিতর্কিত শিক্ষক
বিতর্কিত শিক্ষক


মাঝে মাঝে আমরা ফেসবুক পাড়ায় লেখা চুরির অভিযোগ পাই। কিন্তু জানেন কি আসলে এই লেখা চুরির অভিযোগটা উঠেছিল , আমাদের জাতীয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ও। অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ ভারতের সারস্বত সমাজকে নাড়িয়ে দিয়ে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের বিরুদ্ধে থিসিস চুরির অভিযোগে কলকাতা উচ্চআদালতে মামলা করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য যে গবেষণাপত্রটি ইন্ডিয়ান সাইকলজি অব পারসেপশন প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড জমা দিয়েছিলেন, যদুনাথ সিংহ আর সেই গবেষণাপত্র থেকে ব্যাপকভাবে copy করে ধরা পড়েছিলেন রাধাকৃষ্ণান।
ডঃ যদুনাথ সিংহের গবেষণাপত্রটি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রাধাকৃষ্ণানের "ইন্ডিয়ান ফিলজফি"র দ্বিতীয় খণ্ড, হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল । রাধাকৃষ্ণানের এই বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।ডঃ সিংহ এই চুরির বিষয়টি জানতে পারেন যখন ১৯২৮ সালে রাধাকৃষ্ণানের দ্য বেদান্ত অ্যাকর্ডিং টু শংকর অ্যান্ড রামানুজ নামে আরো একটি বই প্রকাশিত হয়। এই বইটি ছিল রাধাকৃষ্ণনের ইন্ডিয়ান ফিলজফি দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ের একটি স্বতন্ত্র পুনর্মুদ্রণ। যদুনাথ সিংহ দাবি করেন তার গবেষণার প্রথম দুটি অধ্যায় থেকে অনেক অনুচ্ছেদ খ্যাতনামা অধ্যাপক রাধাকৃষন চুরি করেন।
যদুনাথ সিংহ ১৯১৭ সালে এমএ পাশ করেন।প্রেমচন্দ রায়চন্দ স্কলারশিপের আবেদনের সঙ্গে জমা দিয়েছিলেন তাঁর গবেষণাপত্রের প্রথম খণ্ড ১৯২২ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । অভিযোগ, এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় খণ্ড থেকেই অনেকটা নকল করে; রাধাকৃষ্ণ ১৯২৭ সালে তাঁর বই লন্ডন থেকে স্বনামে প্রকাশ করেন। আসলে ওই সময়ে রাধাকৃষ্ণাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন।
ডঃ সিংহ রাধাকৃষ্ণনের এই চৌর্যবৃত্তির ইতিবৃত্ত তুলনামূলক ভাবে মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সিংহপুরুষ যদুনাথ সিংহ মরিসন রিভিউ পত্রিকার মাধম্যে ও কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে রাধাকৃষ্ণনের মতো মহান মানুষের প্রকৃত মুখোশ খুলে দেন।
সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসেবে সারা দেশে পালিত হয়। নিজের জন্মদিনকে এভাবেই নিজের জীবদ্দশাতেই; অমর করে দিয়েছিলেন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। কিন্তু জানেন কি যে দুই খণ্ডের ‘ইন্ডিয়ান ফিলজফি’ বইটির জন্য; রাধাকৃষ্ণণ প্রসিদ্ধ, অভিযোগ সেটি মোটেই তাঁর লেখা নয়। সেটি নাকি লিখেছিলেন; তাঁরই ছাত্র যদুনাথ সিংহ।
১৯২৯ এর জানুয়ারি। মিরাট কলেজের দর্শনের তরুণ অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ, সারা ভারতের শিক্ষা সমাজকে নাড়িয়ে দিয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক অধ্যাপক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের বিরুদ্ধে প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগ তুলে মামলা করে বসলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য জমা দেওয়া যদুনাথের গবেষণা; “ইন্ডিয়ান সাইকলজি অব পারসেপশন” প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড থেকে, ব্যপকভাবে নকল করে ধরা পড়েছিলেন রাধাকৃষ্ণাণ।
যদুনাথ তাঁর অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের জন্য ১৯২৩ সালে গ্রিফিথ পুরস্কার; ১৯২৪ সালে মোয়াট মেডেল ও তার আগে ১৯১৫-১৬ সালে ক্লিন্ট মেমোরিয়াল ও ফিলিপ স্মিথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।
১৯২৫ সালে যদুনাথের গবেষণা শেষ হয়েছিল। আর ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রাধাকৃষ্ণানের বই; “ইন্ডিয়ান ফিলজফি”র দ্বিতীয় খণ্ড। যদুনাথ সুদূর মিরাটে থাকার দরুন কলকাতার শিক্ষা সমাজের সব খবর যথাযথ সময়ে ঠিকঠিক পেয়ে ওঠেন নি। তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পান নি যে; তাঁর মৌলিক গবেষণাটি থেকে রাধাকৃষ্ণান টুকলি করেছেন।
১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কিং জর্জ ফাইভ চেয়ার অফ মেন্টাল অ্যান্ড মোরাল সায়েন্স’ পদে নির্বাচিত হন ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন। মনে রাখা দরকার, সেই সময় দাঁড়িয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ পদটি ছিল দর্শনশাস্ত্রের নিরিখে গোটা ভারতের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ও সম্মানজনক চেয়ার। যদুনাথ সিনহার সেই গবেষণাপত্রটি তিনি সেখানেই পড়েন। এরপরই মিরাট কলেজে অধ্যায়নের জন্য চলে যান যদুনাথ; আর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন নিজের বই তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত বই ‘ইন্ডিয়ান ফিলোসফি’ বিশ দশকের শেষের দিকে বের হয়। মোট দুটি ভলিউমে দেখার চেষ্টা করেন ভারত ভূখণ্ডের দর্শনচিত্রকে।
বিষয়টি তাঁর গোচরে য়াসতেই পরের বছর; অর্থাৎ ১৯২৮ সালে রাধাকৃষ্ণাণের “দ্য বেদান্ত অ্যাকর্ডিং টু শংকর অ্যান্ড রামানুজ” নামে; আরও একটি বই বেরোল। এই বইটি ছিল আসলে “ইন্ডিয়ান ফিলজফি”-র দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ের একটি পুনর্মুদ্রণ। এই বইটি পড়েই যদুনাথ আবিষ্কার করেছিলেন যে, তাঁর গবেষণার প্রথম দুটি অধ্যায় থেকে অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ; নিজের বইতে টুকে বসিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান!
বিখ্যাত “মর্ডার্ন রিভিয়্যু” ইংরেজি পত্রিকার দপ্তরে ক্ষুব্ধ যদুনাথ, সরাসরি রাধাকৃষ্ণাণকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে, দীর্ঘ এক চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন সেই সময়ের । আর তাঁরা এটি প্রকাশ করে।, কারণ রাধাকৃষ্ণাণের “ইন্ডিয়ান ফিলজফি”-র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর, এই পত্রিকাই দেখিয়েছিল যে রাধাকৃষ্ণান তাঁর বেশ কিছু সিদ্ধান্তের পিছনে যথাযথ তথ্যসূত্র উল্লেখ করেনি। তারা সেই নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন ??কিন্তু রাধাকৃষ্ণাণ কোনো জবাব দিতে পারেনি।
তাছাড়া আরো তার প্রমাণ হাতেই ছিল। যদুনাথের গবেষণাকর্মের প্রথম দুই অধ্যায়ের নির্যাস নিয়ে, যদুনাথ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রাধাকৃষ্ণাণের বই প্রকাশিত হওয়ার আগেই, ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে মিরাট কলেজের পত্রিকায় ছাপিয়ে ফেলেছিলেন।
রাধাকৃষ্ণাণ এই খবরটা সম্ভবত রাধাকৃষ্ণাণ জানতেন না। কিন্তু এর ফলে যদুনাথের পক্ষে রাধাকৃষ্ণাণের চুরি প্রমাণ করা খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৯ এর আগস্টে কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয়ে; যদুনাথ স্বত্বাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবী করেন কুড়ি হাজার টাকা।
যদুনাথ সিংহ সুবিচার যদিও পাননি। যদিও শিক্ষাজগতের প্রবীণ সদস্যেরা প্রায় সকলেই যদুনাথের অভিযোগের সত্যতা মেনে নিয়েছিলেন। অনেকেই সহানুভূতিশীলও ছিলেন প্রকৃত বিদ্বান এই মানুষটির প্রতি। কিন্তু সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক মহলে তাঁর প্রতাপের কারণে পরোক্ষ প্রভাবের কারণে যদুনাথ সিংহের উপর তখন নানাভাবে চাপ তৈরি করা হয়েছিল আদালতকক্ষের বাইরে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁদেরই এক অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁদেরই এক গবেষকের মামলা চলছে, তাঁদেরই শিলমোহর পাওয়া গবেষণা নিয়ে। অথচ তাঁরা উচ্চবাচ্যও করেনি।
১৯২৯ এর আগস্টে শুরু হয়ে মামলা চলেছিল ১৯৩৩ এর মে মাস পর্যন্ত। মামলার বিপুল খরচ টানা, তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে উঠছিল।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দু’পক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। যেহেতু মূল সমস্যার মঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়, তাই সেখানেই মিটিয়ে নেওয়া হোক সবটা। মামলার রফা-নিষ্পত্তি হয় আদালতের বাইরে। ১৯৩৩ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস ফণীভূষণ চক্রবর্তীর সামনে; একটি ডিক্রির মধ্যে দিয়ে দুটি মামলা মিটিয়ে দেওয়া হয়। ডিক্রির শর্তগুলি কিন্তু আজও সবার অজানা।